শায়েস্তা খানের আমলে (১৬৬৩-১৬৮৮) ঢাকা বিস্তৃতি লাভ করেছিল পূর্বে পোস্তগোলা, পশ্চিমে জাফরাবাদ-মিরপুর, উত্তরে টঙ্গী আর দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা তো ছিলই। শহরের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এসব জায়গায় বিভিন্ন মোগল স্থাপনা যেমন রাস্তাঘাট, সাঁকো, প্রবেশদ্বার, মসজিদসহ বেসামরিক স্থাপত্যও গড়ে উঠেছিল স্বভাবতই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ঢাকা তার রাজধানীর মর্যাদা হারায়। নতুন রাজধানী স্থাপিত হয় মুর্শিদাবাদে এবং ঢাকা ধীরে ধীরে তার জৌলুস হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজরা পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীদের স্থাপনাসহ সবকিছু এক ধরনের উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতো। ফলে অন্যান্য মোগল স্থাপনার ন্যায় মসজিদগুলোও দুরাবস্থায় পতিত হয়।
সাত গম্বুজ মসজিদ যে মোগল আমলেই নির্মিত— এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যদিও অনেকেই আজকাল ঢাকাস্থ ধানমণ্ডির সাত মসজিদ রোডের নাম শুনলেও যেই মসজিদের নামে এই রাস্তার নামকরণ সেই মসজিদটা কোথায় জানে না। তাদের অবগতির জন্যে বলছি— ঢাকার মোহাম্মদপুরের কাটাসুর থেকে শিয়া মসজিদের দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে বাঁশবাড়ী হয়ে। এই রাস্তাতেই যাওয়ার পথে পড়বে সাত গম্বুজ মসজিদ।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল জাফরাবাদ গ্রামে, নদীর তীরে। নদীটি বুড়িগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাহলে কি মোহাম্মদপুর এলাকার নাম একসময় জাফরাবাদ ছিল? হতেই পারে। তবে প্রকৃতির সেই জৌলুস আর নেই, নেই সেই খোলা প্রকৃতি। নদী কোথায় হারিয়ে গেছে, তার খোঁজ রাখেনি কেউ। মাত্র চার দশক আগেও যারা দেখেছেন, তারা বলবেন তখনও মাদ্রাসার পিছনে নদীর অস্তিত্ব ছিল।
একসময় দূর থেকে এই মসজিদকে দেখে মনে হতো যেন-বা ‘তাজমহল’। অনেকেই একে তখন ‘তাজমহল মসজিদ’ বলে ডাকতেন। আশেপাশে কোনো বাড়িঘর ছিল না। তখন এটিই ছিল ঢাকায় চোখে পড়ার মতো উঁচু স্থাপনা, যা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যেত। তখন মিরপুর ব্রিজে দাঁড়ালে এটি দিব্যি দেখা যেত। মসজিদের পাশেই নদীঘাটে বড় বড় নৌকা এসে ভিড়তো। বর্ষায় পুরান ঢাকা থেকে মানুষজন নৌকা ও বজরায় আর শুকনো মৌসুমে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মসজিদটিতে মানুষজন নামাজ পড়তে আসতেন।
১৮১৪ সালে স্যার চার্লস ডি ওয়াইলির (ঢাকায় অবস্থানকাল ১৮০৮-১৮১১) আঁকা একটি চিত্রকর্ম আছে এই সাত মসজিদকে ঘিরে; যার শিরোনাম— গঙ্গার শাখা নদী বুড়িগঙ্গার তীরের মসজিদটি। এতে দেখা যায়, বুড়িগঙ্গা নদীর পাশেই মসজিদটি দাঁড়িয়ে আছে। নদীর বুকে বয়ে চলেছে নৌকা। ১৯৭৪ সালেও মসজিদটির চারপাশটা পানিতে তলানো ছিল।
অনেকে তখন মসজিদের রেলিংয়ে বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতেন। রেলিংটা ছিল মাটি থেকে অনেক ওপরে। এখন অবশ্য মাটি থেকে হাঁটুর উপরে রেলিং। তখন মসজিদটি মাটি থেকে তিনতলা সমান উঁচু ছিল। এখন মাটি থেকে বরাবর হেঁটে মসিজদে প্রবেশ করা যায়। সে-সময় মসজিদের আশেপাশে একটিমাত্র মাটির পথ ছিল। এখনকার মতো মানুষের ভিড় ছিল না। একেকবার মাত্র পাঁচ থেকে জনা সাতেক লোকের চলাচল দেখা যেত। দুটো পরিচয়হীন কবর ছিল। এখন আরও তিনটি ব্যক্তিগত কবর আছে মসজিদের সামনে।
মসজিদের ছাদে থাকা তিনটি বড় গম্বুজ এবং চার কোণের প্রতি কোণায় জুড়ে থাকা একটি করে অণু-গম্বুজ মিলিয়ে একে সাত গম্বুজ মসজিদ বলা হয়। আসলে একসময় দূর থেকে দেখলে অণুগম্বুজ বা মিনারগুলোকেও গম্বুজই মনে হতো। তবে এর আসল নামটি জানা যায়নি।
মসজিদের দেয়ালে পরিচিতি সংবলিত যে শিলালিপিটি ছিল তাও মুছে গেছে অনেক আগেই। তাই ঠিক কোন সময়ে এবং কে এটি নির্মাণ করেছিলেন তার সঠিক তথ্য নেই। তবে মসজিদটির নির্মাণ শৈলী বিবেচনা করে এর নির্মাণকাল ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি হিসেবে মনে করা হয়। অনেকেই জোর দিয়ে বলেন— ১৬৮০ সালে মোগল সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে তার পুত্র উমিদ খান মসজিদটি নির্মাণ করান। মসজিদটির নির্মাণশৈলী অনেকটাই লালবাগ দুর্গ মসজিদ ও খাজা আম্বর মসজিদের সাথে মিলে যায়।
মসজিদটি শায়েস্তা খানীয় স্টাইলে তৈরি একটি মসজিদ। ছোট হলেও সাতটি আকর্ষণীয় গম্বুজ সহজেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এর আয়তাকার নামাজকোঠার বাইরের দিকের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৭.৬৮ এবং প্রস্থে ৮.২৩ মিটার। এর পূর্বদিকের গায়ে ভাঁজবিশিষ্ট তিনটি খিলান এটিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। দূর থেকে শুভ্র মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। মসজিদের ভিতরে ৪টি কাতারে প্রায় ৯০ জনের নামাজ পড়ার মতো স্থান রয়েছে। মসজিদের পূর্বপাশে এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে একটি সমাধি। কথিত আছে— এটি শায়েস্তা খানের মেয়ের সমাধি। সমাধিটি ‘বিবির মাজার’ বলেও খ্যাত। কবর কোঠাটি ভেতর থেকে অষ্টকোণাকৃতি এবং বাইরের দিকে চতুষ্কোণাকৃতির।
তিন শতাব্দীর বেশি পেরিয়ে গেলেও মসজিদটির অবকাঠামো এখনও প্রায় অবিকৃতই আছে। ১৯৮৮ সালের বন্যায় মসজিদে পানি উঠে গিয়েছিল। সমাধিক্ষেত্রটি পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এরপরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারা প্রথমে মসজিদের সামনের অংশটি পাকা করে এবং তারপর মসজিদের ভেতরের অংশে এবং বাইরে মুসল্লিদের নামাজ আদায়ের স্থানটি মোজাইক করে দেয়। সমাধিটিও এটি সংস্কার করা হয়েছে। তবে পুরাতন যে রঙ ছিল সেই রঙ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সেটা ছিল অনেকটা ইট রঙের মতো কিছুটা খয়েরিও বলা যায় । পরে চুনা সুরকি ছিল। এখন যে রঙ, সেটা আসল রঙ নয়। সংস্কার হলেও বড় ধরনের ভূমিকম্পে টিকিয়ে রাখাই হবে দায়। এরই মধ্যে পুরু দেয়ালে ও ছাদে দেখা দিয়েছে ফাটল।
আগে মসজিদের চারপাশই ছিল ফাঁকা। সামনের অংশে ছিল রাস্তা। এখন সামনের রাস্তাটি আরও প্রশস্ত হয়েছে ঠিকই, বাকি তিন দিকে গড়ে উঠেছে উঁচু দালান। মসজিদের সামনে একটি বড় উদ্যানও রয়েছে। যদিও বর্তমানে গাছ কিছু কাটানো হয়েছে। মসজিদের দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি গ্যারেজ ও চুড়ি তৈরির কারখানা। এগুলোর কালো ধোঁয়ায় মসজিদ যেন নিয়মিতই রঙ বদলায়।
মসজিদ সংলগ্ন মোজাইক করা নামাজের স্থানটি খোলা আকাশের নিচে থাকায় বৃষ্টিতে নামাজরত অবস্থায় যেমন মুসল্লিদের ভিজতে হয় তেমনি সূর্যের তাপে প্রখর রোদে মুসল্লিদের ঘামতে হয়। তাই জুম্মার নামাজের সময় সামিয়ানা টানিয়ে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।
ইংরেজ আমলের বেঙ্গল সার্ভিসের সার্জন ড. জেমস অ্যাটকিনসনকে এই মসজিদ ভেনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ফার্সি জানা অ্যাটকিনসন ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জের (বরিশাল-পটুয়াখালি) শাসনভার পেয়েছিলেন। তিনি ‘অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা’তে মোহাম্মদপুরের সাত গম্বুজ মসজিদের বলছেন— ঢাকার এই মসজিদটি দেখলে ইতালির ভেনিস শহরের কথা মনে পড়ে যায়। কেননা, এটি হঠাৎ করে যেন নদীর তীর থেকে উঠে এসেছে; যা এটিকে দিয়েছে অপূর্ব চিত্রের বিষয়োপযোগিতা। অযত্ন-অবহেলায় এবং দুর্ঘটনা ও সময়ের অত্যাচারে এর খিলান আর গম্বুজ আজ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম। তারপরও মসজিদটির নির্মাণ কৌশলে সাধারণ পরিমিতিবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্থপতির সৌন্দর্যবোধ ও প্রতিভা প্রশংসা করবার মতো। সময়ের করাল গ্রাস, আগাছা, ঝড়-বাদল ও রৌদ্রতাপ শুধু যে এর বর্ণবৈচিত্র্য বাড়িয়েছে তা কিন্তু নয় সেই সঙ্গে বর্ণের উজ্জ্বলতায় কমনীয়তা এনেছে। এতে করে আজও এখানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় আছে।













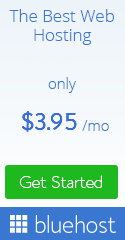
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন